বর্তমান ব্যবস্থায় সংসদীয় এলাকা অনুসারে প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাতে দেখা যায়, এলাকার আকৃতি ও ভোটারের সংখ্যার তারতম্যের ভিত্তিতে একেকজন প্রার্থী একেকটি এলাকা থেকে বিজয়ী হন, একটি দলের মোট আসন সংখ্যার ভিত্তিতে দলটি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, যদিও সারা দেশে প্রাপ্ত মোট ভোটের অনুপাতে সেই দলটিই হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের সমর্থন পায়নি। এমন নজির বিগত নির্বাচনগুলোতে আমরা একাধিকবার দেখেছি। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি’র পক্ষে ভোট পড়েছিলো ৩০.৮১%, অপর দিকে আওয়ামী লীগ পেয়েছিলো ৩০.০৮% ভোট। ফলে জনসমর্থনের বিচারে দুই দল সমানে সমান হলেও আসন সংখ্যায় বিএনপি (১৪০) ছিল আওয়ামী লীগের (৮৮) চেয়ে অনেক অনেক এগিয়ে।
১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ (১৪৬ আসন) বিজয়ী হয় ৩৭.৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে, বিএনপি (১১৬ আসন) ৩৩.৬১ শতাংশ ভোট পেয়ে জনসমর্থনে তেমন পিছিয়ে না থাকলেও আসন সংখ্যার বিচারে অনেক পিছিয়ে যায়। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপির প্রাপ্ত মোট ভোট আবারও আওয়ামী লীগের চেয়ে খুবই সামান্য বেশি থাকলেও (যথাক্রমে ৪০.৯৭ ও ৪০.১৩ শতাংশ) আসন সংখ্যায় তারা ছিল আওয়ামী লীগের ধরাছোঁয়ার বাইরে (যথাক্রমে- ১৯৩ ও ৬২)। ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি ভোট পায় ৩২.৫০ শতাংশ, কিন্তু তারা মোট আসন লাভ করে মাত্র ৩০টি; অপর দিকে জাতীয় পার্টির প্রাপ্ত ভোট ছিল মাত্র ৭.০৪ শতাংশ। কিন্তু তারা আসন লাভ করে ২৭টি! অর্থাৎ, জাতীয় পার্টির চেয়ে প্রায় ২৫ শতাংশের চেয়েও বেশি ভোট পাওয়ার পরও বিএনপির আসন ছিল মাত্র ৩টি বেশি! অপর দিকে, ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত নির্বাচনগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বিজয়ী দলগুলো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও সারা দেশের মোট ভোটারের ৫০ শতাংশ সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়েছে। আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনে সর্বোচ্চ ৪৮.০৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিলো; যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ।
১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ধরে নিলে, এই তিনটি নির্বাচনের বিজয়ী দলের জনসমর্থন যথাক্রমে ৩০, ৩৭ ও ৪০ শতাংশের কিছু বেশি। অর্থাৎ, এই তিনটি নির্বাচনে মোট ভোটারের যথাক্রমে ৭০, ৬৭ ও ৬০ শতাংশ ভোটার বিজয়ী দলগুলিকে সমর্থন করেনি। অন্য কথায়, সিংহভাগ ভোটার চায়নি এই দলটি সরকার গঠন করুক। যদি নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাবো, ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনেই, দেশের অন্তত অর্ধেক ভোটার নির্বাচনে বিজয়ী দলটিকে সমর্থন দেয়নি! আইনের মারপ্যাঁচে উৎরে গেলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা আর যাই হোক ‘জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে’ দেশ চালানো নয়।
এই সমস্যার সমাধানকল্পে, জাতীয় সংসদের গঠন-পদ্ধতিগত এবং কাঠামোগত পরিবর্তন আবশ্যক। প্রথমত, সংসদের আসন বিন্যাস হবে একেকটি দলের প্রাপ্ত মোট ভোটের শতকরা হিসাব অনুসারে, একেকটি সংসদীয় এলাকায় কে কত হাজার ভোট পেলেন তার ভিত্তিতে নয়। নির্বাচনের যথেষ্ট আগে একেকটি দল তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে। সেই তালিকায় অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রার্থীদের নাম উল্লেখ করা থাকবে। একেকজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, নাগরিক পরিচিতি, সামাজিক পরিচিতি, পেশাগত পরিচিতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি ওই তালিকায় উল্লেখ করতে হবে। সারা দেশে একযোগে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে প্রাপ্ত মোট ভোটের শতকরা হিসাব অনুসারে একেকটি দল সংসদে আসন বরাদ্দ পাবে। সংসদের মোট আসন সংখ্যা যদি ৩০০টি হয়ে থাকে, তাহলে প্রতি ১ শতাংশ ভোটের জন্য একটি দল ৩টি আসন বরাদ্দ পাবে। অর্থাৎ ৩ জন এমপি তাদের দল থেকে সংসদে যাবে। তাদের প্রকাশিত তালিকার প্রাধিকারের ভিত্তিতে ওই ৩ জনকে তারা মনোনীত করবে। এভাবে, সরকার গঠনের জন্য ন্যূনতম সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য কোনও দলকে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেতেই হবে; অন্যথায় কোয়ালিশন সরকার গঠন করা ছাড়া উপায় থাকবে না।
কোন এলাকার ভোটাররা কোন দলটিকে বেশি ভোট দিয়েছে, তা ভোট গ্রহণ ও গণনার পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটি দল তাদের মোট প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে যে ক’টি আসন বরাদ্দ পাবে; অঞ্চলভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তারা সেই আসনের জন্য সাংসদ মনোনীত করবে। অর্থাৎ জাতীয় পার্টির মোট প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে যদি আসন বরাদ্দ হয় ১০টি এবং তাদের অধিকাংশ ভোট যদি রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও গাইবান্ধা জেলা থেকে আসে, তাহলে তারা তাদের ১০ জন এমপি প্রেরণ করতে ওই চার জেলার ১০টি আসনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।
এই হলো গঠন-পদ্ধতিগত সংস্কার প্রস্তাব। এবার কাঠামোগত সংস্কারের দিকে আলোকপাত করা যাক।
জাতীয় সংসদ যেহেতু দেশের আইন সভা, এর সদস্যদের কেবল এবং কেবলমাত্র আইন, বিধিবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। স্থানীয় সরকার একটি পৃথক বিভাগ; যা পরিচালিত হয় নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা। আইনসভার অতি-সম্মানিত সদস্যদের স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে জড়িত হওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে। এলাকার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, অবকাঠামো, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি দেখার জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ আছেন। উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ উপজেলা ও জেলায় নিযুক্ত বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ স্থানীয় সরকারের সকল কাজকর্ম সামলাবেন। সংসদ সদস্য কেবল জাতীয় ইস্যু নিয়ে কাজ করবেন। তিনি নিয়মিত আইনসভার অধিবেশনে যোগ দেবেন। অধিবেশন স্থগিত থাকাকালে বিগত অধিবেশনের এজেন্ডা বাস্তবায়নের কাজ করবেন, আগামী অধিবেশনে উত্থাপনযোগ্য বিল নিয়ে কাজ করবেন। সংসদে পাস হওয়া আইন, বিধান ও আদেশ নির্দেশ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো পালন করেছে কি করছে না, তা তদারক করবেন - অবশ্যই ‘সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে’ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে; কোনও সংসদীয় এলাকায় গিয়ে নয়। স্থানীয় জনগণ বা ভোটারগণ তাদের নির্বাচিত এমপি’র কাছে কোনও দাবিদাওয়া পেশ করবেন না, প্রত্যাশা রাখবেন না। তারা কেবল দেখবেন - আইন প্রণয়নের কাজে এই প্রার্থী কতটা যোগ্য; তাতে রাস্তা মেরামত বা ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণে প্রার্থীর যোগ্যতা না থাকুক, কিছু আসে যায় না। সংসদ সদস্য একজন আইনবিদ হলে ভালো, অন্তত আইন বুঝতে পারার মতো যথেষ্ট শিক্ষিত তাঁকে হতেই হবে; ঠিকাদারি করা তাঁর কাজ নয়। প্রার্থীদের কোনও দাবিদাওয়া না শুনলে, কোনও আশ্বাস না দিলে তারা ওই প্রার্থীকে ভোট দেবে কেন? তারা তো প্রার্থীকে ভোট দেবে না, ভোট দেবে ওই প্রার্থীর দলকে, ব্যক্তি হিসেবে প্রার্থীকে নয়।
সংসদীয় আসন সারা দেশেই বণ্টন করা হবে যদিও, কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তিকেই ওই আসনের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে - এমন কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এটা অবশ্য এখনকার বিদ্যমান আইনেও নির্দিষ্ট করা নেই। যে কারণে আমরা গোপালগঞ্জের শেখ হাসিনাকে রংপুরের প্রার্থী হতে দেখেছি, রংপুরের এরশাদ এমপি হয়েছেন ঢাকার আসন থেকে। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসন তাদের এলাকার উন্নয়নমূলক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের জন্য এমপির নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন, তারা মাসিক বা ত্রৈমাসিক রিপোর্ট দাখিল করবেন; কিন্তু সেই রিপোর্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে কেন্দ্রে প্রেরণ করা হবে, সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্য নিজ এলাকায় গিয়ে নয়; বরং জাতীয় সংসদে স্থাপিত কার্যালয়ে বসে সেই নথি দেখবেন ও মূল্যায়ন করবেন। সংসদ সদস্য কোনোভাবেই দেশের কোনও এলাকায় প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পাবেন না। নোয়াখালী জেলার বাসিন্দা যদি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় জেলাপ্রশাসকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, বরিশালের বাসিন্দা যদি সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপারের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, তাহলে প্রত্যেক উপজেলা থেকে এমপি নির্বাচিত করার কোনও আবশ্যকতা নেই। নেতৃত্ব সারা দেশ থেকেই আসবে; কিন্তু সেই নেতৃত্বকে স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব না করে বরং জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পদে অর্থাৎ ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, উপজেলা চেয়ারম্যান/মেম্বার, পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের মেয়র/কাউন্সিলর ইত্যাদি পদে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তারা স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হবেন। এই স্তরে সাফল্য দেখানোর মাধ্যমে তারা স্থানীয় থেকে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। যদি স্থানীয় পর্যায়ে সফল হতে না পারেন; জাতীয় সংসদের দ্বার তাদের জন্য খুলবে না।
একজন এমপির মর্যাদা হবে একজন মন্ত্রীর চেয়ে বেশি। কেননা একজন মন্ত্রী তার সকল কর্মকাণ্ডের জন্য সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। প্রত্যেক মন্ত্রীকে তার মন্ত্রণালয়ের মাসিক কর্মসূচির তালিকা সংসদের কাছে পেশ করতে হবে। মাস শেষে সেই তালিকার অগ্রগতির রিপোর্ট দাখিল করতে হবে, বরাদ্দকৃত অর্থছাড়ের হিসাব প্রতিমাসে হালনাগাদ করতে হবে। প্রকল্পের মোট ব্যয় কত টাকা; তার থেকে কত টাকা ছাড় করা হয়েছে; ছাড় করা টাকার কত শতাংশ কোন খাতে ব্যয় হয়েছে; কত টাকা মন্ত্রণালয়ের তহবিলে জমা থেকে গেছে; কাজের অগ্রগতি কত শতাংশ; প্রাক্কলিত অগ্রগতির সাথে তা কতটা বেশি বা কম বা যথাযথ কিনা - এসব রিপোর্ট প্রতি মাসে সংসদে হালনাগাদ করতে হবে। সংসদ যদি কোনও মাসে অধিবেশনে না থাকে; তাহলে তা সংসদ সচিবালয়ে জমা পড়বে এবং স্পিকার/ডেপুটি স্পিকার ও সংসদ সচিব তা মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নপত্রে স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এবং উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সেই মাসের বেতন ছাড় করা হবে না।
সংসদ সদস্য পদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার নির্দিষ্ট করতে হবে। তাদের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি। বিদ্যমান ব্যবস্থায় একজন এমপি যেভাবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার চর্চা করেন; লাল পাসপোর্ট ব্যবহার করেন; ট্যাক্স-ফ্রি গাড়ি আমদানি করেন; স্থানীয় উন্নয়নের সকল বরাদ্দ নিজের হাতে কুক্ষিগত রাখতে পারেন - এই অসীম ক্ষমতায় লাগাম পরাতে হবে। ‘আইন-প্রণেতা’ কোনও লাভজনক পদ হতে পারে না, লোভনীয় পদ হতে পারে না। আইন প্রণয়ন যার কাজ; তিনি নিজেই যদি নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে বলে মনে করতে থাকেন; তাহলে আইনের শাসন কোনোদিন বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। মাইকেল ফ্যারাডে যখন প্রথম বিদ্যুৎ শক্তি আবিষ্কার করলেন; তখন তিনি সেই বৈদ্যুতিক তার হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন - এটা আমার আবিষ্কার, তাই আমাকে সে শক দেবে না। কিন্তু এক ঝটকায় ভূপাতিত হওয়ার পর তার বোধদয় হয় - শক্তি কখনও পক্ষপাত করে না। একই কথা আইনসভার সদস্যদের জন্যও কড়াকড়িভাবে প্রযোজ্য।
আইন প্রণয়ন করছেন বলেই তাঁরা ইচ্ছামতো সেই আইনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারেন না। বরং আইন-প্রণেতা হিসেবে দেশের অন্য যেকোনও নাগরিকের চেয়ে তাদেরকেই সবচেয়ে বেশি মেনে চলতে হবে নিজেদের তৈরি আইন। মনে রাখতে হবে, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যবর্তী একটি গ্রে-এরিয়াতে তাদের অবস্থান। তাই উভয় দিকের সমতা বিধান করার মূল দায়িত্বটা তাদেরই।
লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক
ভোরের আকাশ/রন
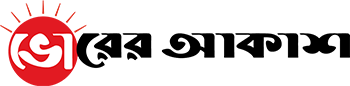
















মন্তব্য